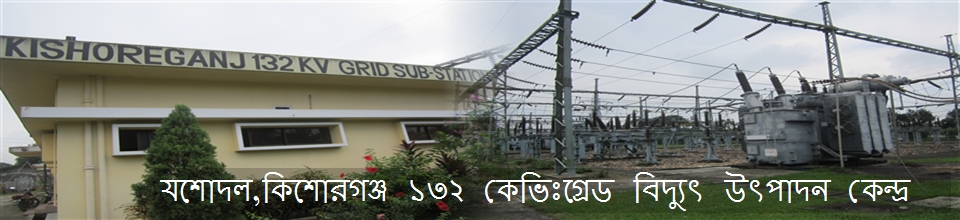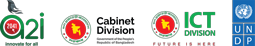-
ইউনিয়ন সম্পকিত
ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক
-
ইউনিয়ন পরিষদ
ইউনিয়ন পরিষদ
ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম
গুরুত্ব পূর্ণ তথ্য
-
সরকারী অফিস
ভূমি
স্বাস্থ্য সেবা
সমাজসেবা
-
অন্যান্য প্রতিষ্ঠান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
সংগঠন
- বিভিন্ন তালিকা
- প্রকল্প
- সেবা সমূহ
- গ্যালারি
-
ইউনিয়ন সম্পকিত
ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক
-
ইউনিয়ন পরিষদ
ইউনিয়ন পরিষদ
ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম
গুরুত্ব পূর্ণ তথ্য
-
সরকারী অফিস
ভূমি
স্বাস্থ্য সেবা
সমাজসেবা
-
অন্যান্য প্রতিষ্ঠান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
সংগঠন
- বিভিন্ন তালিকা
- প্রকল্প
- সেবা সমূহ
-
গ্যালারি
ফটো গ্যালারি
ভিডিও গ্যালারি
বাতায়নের যশোদল ইউনিয়নের ঘটনা প্রবাহ
মানুষের সমাজবদ্ধতার সাথে ভাষার উদ্ভব জড়িত, কারণ পরস্পরের কাছে মনের ভাব ব্যক্ত করার জন্যই ভাষার আবশ্যিকতা। সংস্কৃতির সাথে রয়েছে ভাষার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। আঞ্চলিক ভাষা বিকশিত হয় কোন নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। যশোদল সাংস্কৃতিক অঞ্চলে স্বতন্ত্র হয়েছে পূর্ব দিকে বৌালাই ইউনিয়ন। যে অঞ্চলের সীমানায় দক্ষিণ দিকে কশা কড়িয়াল ইউনিয়ন, উত্তর দিকে কিশোরগঞ্জ শহর, চৌদ্দশত ইউনিয়ন। কিছু কিছু অমিল থাকার পরও এই সাংস্কৃতিক অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা, প্রবাদ প্রবচন ও লোকগাঁথায় বেশকিছু মিল পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ মেলামেশায় জাতি যেমন সংকর হয়ে ওঠে মানুষে মানুষে মেলামেশায় ভাষাও তেমনি সংকর হয়ে ওঠে এবং এভাবেই উপভাষার চরিত্র কখনও বিপন্ন হয়ে যায়। সাংস্কৃতিক অঞ্চলটি সে অর্থে অনেকটাই নিরাপদ।
ইউনিয়নেরআঞ্চলিক/স্থানীয়ভাষা লগে লগে বাঘা বাগদি আয়া কইল “ফটিকদা, মা ডাকতাছে”। ফটিক কইল “যাইতাম না”। বাঘা তারে জোড় কইরা কোল তুইল্যা লয়্যা গেল, ফটিক কিছু না পাইরা রাগের চোটে আত-পাও লাড়াইতাছিল। ফটিকরে দেইকখাই তার মা আগুনের মূর্তির লাহান হইয়া গেল, কইল “আবার তুই মাখনরে মারছস” ফটিক কইল “না মারছিনা”। “হিরেবারমিছা কথা কস”। “কুনো সমুই মারছিনা। মাখনরে জিগাও”।
প্রচলিতবুলি, বচন, কৌতুক, জোকস, প্রবাদবাক্য
ধারায় নারা বাইরায়, চৌদ্দ পুরুষ তার পেন্দে দৌড়ায়
[পূর্বপুরুষদের কাজ/অভ্যাস এর প্রভাব পরবর্তীদের মধ্যে ও র্দীঘদিন বহাল থাকে।]
এক পয়সার ঋণের লাইগ্যা চান্দেরে খাইল
[চন্দ্র্রগ্রহনের বেলায় প্রযোজ্য, বলা হতো যে, সূর্য এক পয়সা ঋনের জন্য চন্দ্রকে গ্রাস করছে।]
শিলে পাডায় ঘষাঘষি, মইচের জীবন শেষ
নাইড়্যা মাথায় টিনটিন, এক পয়সার তেলের টিন
[ছোট ছেলের মেয়ের মাথা ন্যাড়া করলে, তার বন্ধুরা তাকে খ্যাপানো জন্য বলে থাকে]
আইলসার ডাহুর [অত্যন্ত অলস], বলদ [বোকা অর্থে], লুহুনদরা [অলস], বাপের বেডা [সাহসী], চোপা করা [মুখে মুখে তর্ক করা] ইত্যাদি।
লোকসংস্কৃতি, লোকউৎসব, লোকসংগীত, লোকগাঁথাঃ
লোক সংস্কৃতি,লোক উৎসব, লোকসংগীত, লোকগাঁথার দিক দিয়ে যশোদলইউনিয়ন হলো প্রসিদ্ধ। রয়েছে কাজলরেখা, সফর মুল্লুক, রুপবান, ইত্যাদি পালা।
তাছাড়া যাত্রাগান, গ্রামীণ কাহিনীর উপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠিত নাটক ও যাত্রা সালুয়া ইউনিয়নের ঐতিহ্য। যশোদল ইউনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকসঙ্গীতগুলোর অন্যতম হলো বাউলগান, ভাটিয়ালী, কিস্সাপালা, কবিগান, কীর্তন, ঘাটুগান, জারিগান, সারিগান, মুর্শিদী, যাত্রা, বিয়ের গান, মেয়েলীগান, বিচ্ছেদী গান, বারমাসী, পুঁথিগান, পালকির গান, ধানকাটার গান, ধানভানার গান, হাইট্টারা গান, গাইনের গীত, বৃষ্টির গান, ধোয়া গান, শিবগৌরীর নৃত্য গীত, গাজীর গান, পটগান ইত্যাদি ।
প্রধানপ্রধানউৎসবঃ
নবান্ন: যশোদল ইউনিয়নে সুদূর অতীত হতে নতুন ধান উঠা উপলক্ষ্যে নবান্ন উৎসব প্রতি ঘরে ঘরে পালিত হয়ে আসছে। অগ্রহায়ন মাসে নতুন ফসল ঘরে উঠানোর পর ঐতিহ্যবাহী খাদ্য পরিবেশনের নামই হলো নবান্ন। নবান্নে পিঠা পার্বণের সাথে সাথে পুরনো কিচ্ছা, কাহিনী, গীত, জারি এই সবকে উপজীব্য করে চলে রাত্রীকালীন গানের আসর।
পিঠাউৎসব: অগ্রহায়ন পৌষের শীতে নবান্নের পিঠা-মিষ্টি উৎসবের সময় সালুয়া ইউনিয়নের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এক উৎসব মুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে। নানা ধরনের পিঠার মধ্যে রয়েছে তেলের পিঠা, মেরা পিঠা, পাটি সাপটা, মসলা পিঠা, পুলি পিঠা, গুলগুল্যা পিঠা, দই পিঠা, ভাপা পিঠা, দুধ কলা পিঠা, চিতল পিঠা, খেজুর রসের পিঠা, নকসী পিঠা ইত্যাদি।
নববর্ষওমেলা:
যশোদল ইউনিয়নের গ্রামাঞ্চলে এখনও শহরের মতো বর্ষবরণের প্রচলন শুরু না হলেও অতিপ্রাচীনকাল হতে এখানে বিরল অথচ লোকজ ঐতিহ্যের দাবী নিয়ে দীপশিখা জ্বালিয়ে বাংলা বর্ষ বিদায়ের এক নীরব আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হতো। মেলা উপলক্ষে মহিলারা বাপের বাড়ীতে নাইয়র আসত এবং মেলায় এসে ছোট বাচ্চারা খেলনা, বাঁশি, কিনতো। মেলায় বিভিন্ন রকম সার্কাস, দোলনা খেলা চলতো।
যাত্রাগান:
সাধারনত শীতকালে প্রাচীন লোককাহিনীর উপর ভিত্তি করে যাত্রার আয়োজন করা হয়। এই সব যাত্রা এবং যাত্রাগান কখনো কখনো রাতব্যাপী হয়ে থাকে। যেসব কাহিনী/বিষয়ের উপর ভিত্তি করে যাত্রা হয় তমধ্যে কাজল রেখা, সফর মুল্লক, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা এবং স্থানীয় ভাবে রচিত বিভিন্ন কাহিনী/উপাখ্যান অন্যতম।
পালাগান:বর্তমানে পালাগানের আয়োজন হয় না বললেই চলে। তবে পূর্বে বিভিন্ন স্থানে পালাগানের আয়োজন করা হতো।
বিয়ে/জম্মদিন/বিবাহবার্ষিকীরআনুষ্ঠানিকতাসংক্রান্তঃ
বাংলাদেশের অন্যান্য ইউনিয়নের মতোই সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই সালুয়া ইউনিয়নে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে জম্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী পালনের প্রচলন আগে তেমন না থাকলেও ইদানিং মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের মাঝে তা ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে। বিয়েতে বরের পক্ষ থেকে বরযাত্রী যায় কনের বাড়ীতে। কনের বাড়ীতে বরযাত্রীদের গায়ে রং ছিটিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ বহুদিনের, এই নিয়ে ঝামেলাও কম হয় না। বরপক্ষের আনা জিনিস পত্র নিয়ে ঘাটাঘাটি, সমালোচনা, রসাত্মক আলোচনা চলে কনে পক্ষের লোকজনের মধ্যে। খাওয়া-দাওয়া ও বিয়ে শেষে কনেকে বরের বাড়ীতে নিয়ে আসা হয়, সেখানে মহিলারা অপেক্ষা করেন ধান, দূর্বা, চিনি ইত্যাদি নিয়ে কনেকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য। পরের দিন বৌভাত অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত দুই-তিন দিন পর বর ও কনে মেয়ের বাড়ীতে বেড়াতে যায়, যাকে ‘ফিরানী’ বলা হয়। কয়েক দিন সেখানে থেকে পুণরায় বর নিজের বাড়ীতে ফিরে আসেন।
প্রচলিতখেলাধুলা, খেলাধুলারবিবর্তন
পূর্বে এ অঞ্চলে প্রধান আমোদ প্রমোদ ছিল ঘুড়ি উড়ানো, নাচগান, লীলা ও তাস খেলা, নৌকাবিহার, পাশা খেলা, বানর লম্ফ, মোরগ লড়াই, দাড়িয়াবান্দা, কাবাডি, ক্যারম, গোল্লাছুট, দাবা, ব্যাডমিন্টন, ফুটবল, বৌচি ইত্যাদি। গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্দা, কাবাডি, মোরগ লড়াই ইত্যাদি খেলার স্থান ক্রমে দখল করে নিয়েছে ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলা। প্রযুক্তির উন্নতির দরুন টেলিভিশনের মাধ্যমে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ফুটবল ক্রিকেট খেলা গ্রাম ও শহরে সমানভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই আজ বেশিরভাগ মাঠই দাড়িয়াবান্দা, হা-ডু-ডু, বৌচি, গোল্লাছুট ইত্যাদির পরিবর্তে
একনজরে ৫ নং যশোদল ইউনিয়ন পরিষদঃ
১। ইউনিয়নের নামঃ ৫ নং যশোদল ইউনিয়ন পরিষদ
২। মোট জনসংখ্যাঃ (ক) পুরুষঃ ১৪,৬৬৩ জন।
(খ) মহিলাঃ১৪,০৬৯ জন।
সর্ব মোটঃ২৮, ৬৬৩জন।
গ্রাম অনুসারে লোক সংখ্যার তথ্য:
|
ক্রমিক |
গ্রামের নাম |
পুরুষ |
মহিলা |
মোট |
|
১ |
আমাটিশিবপুর |
৭৬৯ |
৭০২ |
১৪৭১ |
|
২ |
বীরদামপাড়া |
৯৬৯ |
৯৯০ |
১৯৫৯ |
|
৩ |
বিষ্ণুবাড়ী |
৩৩ |
৩৭ |
৭০ |
|
৪ |
ব্রাক্ষনকান্দি |
৭৫৪ |
৭৩৫ |
১৪৮৯ |
|
৫ |
দামপাঠুলী |
৩৭৯ |
৩৪৩ |
৭২২ |
|
৬ |
ঘাগৈর |
৩৬২ |
৩৪৯ |
৭১১ |
|
৭ |
ঘোষেরকান্দি |
১৫৮ |
১৩৮ |
২৯৬ |
|
৮ |
যশোদল |
৪১৭৯ |
৪০০৪ |
৮১৮৩ |
|
৯ |
মনিপুরঘাট |
৬৯৮ |
৭১৪ |
১৪১২ |
|
১০ |
কাটাখালী |
৬২০ |
৫৭৩ |
১১৯৩ |
|
১১ |
বানিয়াকান্দি |
৬৪২ |
৬০১ |
১২৪৩ |
|
১২ |
মুসলিমপাড়া |
৩৬৩ |
৩৫৯ |
৭২২ |
|
১৩ |
মীরপাড়া |
৪৩৪ |
৪৪৬ |
৮৮০ |
|
১৪ |
মধ্যপাড়া |
৫৪৪ |
৫০৮ |
১০৫২ |
|
১৫ |
গোয়ালাপাড়া |
৪৪৪ |
৪১৮ |
৮৬২ |
|
১৬ |
রায়পাড়া |
৪৩৪ |
৩৮৫ |
৮১৯ |
|
১৭ |
কালিকাবাড়ী |
৬০৪ |
৫৮০ |
১১৮৪ |
|
১৮ |
কুতকাইল |
৫৬৬ |
৫৪১ |
১১০৭ |
|
১৯ |
মধুনগর |
৫৪০ |
৫৬১ |
১১০১ |
|
২০ |
স্বল্প দামপাড়া |
৩৮৬ |
৩৩৬ |
৭২২ |
|
২১ |
স্বলাপ যশোদল |
৪৯০৫ |
৪৭৪৩ |
৯৬৪৮ |
|
২২ |
ধলিয়ারচর |
৭৪৪ |
৬৩৪ |
১৩৭৮ |
|
২৩ |
নধার |
১০০২ |
৯৪৫ |
১৯৪৯ |
|
২৪ |
ভুবিরচর |
১১১৩ |
১১৩৭ |
২২৫০ |
|
২৫ |
ভাবুন্দিয়া |
৪৯৪ |
৫১০ |
১০০৪ |
|
২৬ |
বাগপাড়া |
২১৬ |
১৯০ |
৪০৬ |
|
২৭ |
ইছাশুর |
৫৬৭ |
৫৮৮ |
১১৩৫ |
|
২৮ |
কোনামাটি |
৩৮৮ |
৪০২ |
৭৯০ |
|
২৯ |
নোয়াপাড়া/ খাসপাড়া |
৩৮১ |
৩৫৭ |
৭৩৮ |
৩। আয়তনঃ ১৬.৫০বর্গ কিলোমিটার।
৪। ফসলি জমির পরিমানঃ (ক) মোট ভূমির পরিমান:১৪৩৫ হেক্টর।
(খ) আবাদি ১২৪২ হেক্টর
(গ) জলাশয় ৫৫ হেক্টর।
(ঘ) স্থায়ী পতিত ১০০ হেক্টর।
(ঙ) সাময়িক পতিত ১৭ হেক্টর।
(চ) স্থায়ী ফল বাগান ১২ হেক্টর।
(ছ) স্থায়ী বন ১০ হেক্টর।
মোট কৃষি পরিবার ৬৩৫৯ টি।
ভূমিহীন কৃষি পরিবার ৩৫২২ টি
প্রান্তিক কৃষি পরিবার ১৪৫৯ টি
ক্ষুদ্র ক্রষি পরিবার ১০২০ টি
মাঝারি কৃষি পরিবার ৩১৯ টি
বড় কৃষি পরিবার২৯ টি
উৎপাদিত কৃষি পন্য সমূহ: ধান,গম,ভুট্রা,পাট,পেপে,আলু,কলা,বিবিন্ন প্রকার শাক সবজি।
কৃষি ব্লক সংখ্যা ৪টি।(যশোদল,বীরদামপাড়া,কাটাখালী,নধার)
৫। শিক্ষার হারঃ ৬২.১২%
৬. উচ্চ বিদ্যালয়ঃ ২টি।
৭। প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ ১৪ টি। ( সরকারী ৭টি, রেজিঃ ৭টি)
৮। মাদ্রাসাঃ ৫টি। (হাফিজিয়া মাদ্রাসা)
৯। মক্তবঃ ১২ টি।
১০। মসজিদঃ ৪০টি।
১১। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রঃ ১টি
১২। ডাকঘরঃ ৩টি।
১৩। হাটবাজারঃ ৩টি।
১৪। রেলওয়ে ষ্টেশনঃ ১টি।
১৫। মৌজা সংখ্যাঃ ১৪টি।
১৬। গ্রামের সংখ্যাঃ ২৯টি।
১৭। মোট খানার সংখ্যাঃ ৬,১১৪টি।
১৮। মন্দিরের সংখ্যাঃ ২টি।
১৯। তহসিল অফিসঃ ১টি।
২০। ব্যাংক সংখ্যাঃ ১টি।
২১।সেচ ব্যবস্তাঃ
ক) গভীর নলকূপঃ ১৩টি।
খ) পাওয়ার পাম্প ১৫টি।
২২। মৎস্য সংবাদঃ
ক) চাষ উপযোগী মৎস্য পুকুর (ব্যক্তিগত)-৩২৫টি।
খ) মৎস্য খামারঃ ২০টি।
২৩। ইউনিয়েনর নদী/খালঃ
ক) নদী(অনাব্য)৩.৫০ কিলোমিটার
খ) খাল (অনাব্য) ৬.০০ কিলোমিটার।
২৩। যাতায়ত ব্যবস্তাঃ
ক) পাকা রাস্তাঃ৩০ কিলোমিটার
খ) কাচা রাস্তাঃ৩৫ কিলোমিটার
গ) রেল লাইনঃ ৪কিলোমিটার
ঘ) পাকা ব্রীজঃ ১০টি(১টি নির্মানাধীন)
ঙ) কালভার্টঃ ৭৫টি
২৪। ইউনিয়ন পরিষদের মাসিক সভার তারিখঃ প্রতি ইংরেজী মাসের ১০ তারিখ।
২৫। গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সদস্য সংখ্যাঃ ২৮ জন।
২৬। আনসার প্লাটুনঃ ৩২ সদস্য বিশিষ্ট (সক্রিয়)
২৭। সুতার কলঃ ১টি(বন্ধ)
২৮। শিল্প কারখানাঃ
ক) চাউল কলঃ ১২টি
খ) স,মিলঃ ৮টি
গ) আইসক্রীম ফ্যাক্টরীঃ ১টি
ঘ) বেকারীঃ ৪টি।
২৯। সরকারী কবরস্তানঃ ১টি
৩০। গাভী প্রজনন কেন্দ্রঃ ১টি
৩১। পানির পাম্পঃ ১টি(নির্মানাধীন)
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস